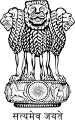পূর্ব দক্ষিণ এশিয়া
| পূর্ব দক্ষিণ এশিয়া | |
|---|---|
 দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্রে পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান | |
| আয়তন | ১০,১৪,৮৭২ কিলোমিটার (৬,৩০,৬১২ মাইল) |
| জনসংখ্যা | ৫৬,৫৬,৬২,১৪৭ (২০২২) |
| জনঘনত্ব | ৫৫৭ প্রতি বর্গকিলোমিটার (১,৪৪০ প্রতি বর্গমাইল) |
| ধর্ম | হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম |
| দেশ | |
| ভাষা | সবচেয়ে প্রচলিত: |
| সময় অঞ্চল | ইউটিসি+০৫:৩০, ইউটিসি+০৫:৪৫, ইউটিসি+০৬:০০ |
| ইন্টারনেট টিএলডি | .ইন, .বিডি, .এনপি, .বিটি |
| বৃহত্তম শহর | ঢাকা |
| ধর্ম | হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম |
| নৃগোষ্ঠী | ইন্দো-আর্য, তিব্বতি-বর্মীয়, খাসি |
পূর্ব দক্ষিণ এশিয়া[১][২][৩] দক্ষিণ এশিয়া উপঅঞ্চলের পূর্বদিকে অন্তর্গত একটি ভৌগোলিক অঞ্চল। বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল ও ভারত (বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারত) এই অঞ্চলের অন্তর্গত। ভৌগোলিকভাবে এটি পূর্ব হিমালয় ও বঙ্গোপসাগরের মাঝে অবস্থিত। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র (যমুনা), বিশ্বের দুই বৃহত্তম নদী, এই অঞ্চল দিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়। বিশ্বের সর্বোচ্চ পার্বত্য এলাকা ও বিশ্বের সবচেয়ে বড় ব-দ্বীপ এই অঞ্চলের অন্তর্গত এবং এই অঞ্চলের জলবায়ু আল্পীয় থেকে উপ-ক্রান্তীয় ও ক্রান্তীয় পর্যন্ত হতে পারে। নেপাল, ভুটান ও উত্তর-পূর্ব ভারত স্থলবেষ্টিত হওয়ার জন্য বাংলাদেশ ও পূর্ব ভারত এই অঞ্চলের প্রবেশদ্বার।
পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ার জনসংখ্যা ৪৪ কোটির বেশি, য বিশ্বের ৬% জনসংখ্যা এবং দক্ষিণ এশিয়ার ২৫% জনসংখ্যা। বিবিআইএন সংযুক্তি এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক একত্রীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। এই অঞ্চলের চারটি দেশ (বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল ও ভারত) দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা ও বিম্সটেকের সদস্য। চীনের ইউন্নান প্রদেশ ও তিব্বত স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল এবং মিয়ানমার ঐতিহাসিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে ও সাংস্কৃতিকভাবে পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ার সাথে সম্পর্কিত। বাংলদেশ–চীন–ভারত–মিয়ানমার ফোরাম এই অঞ্চলে এক অর্থনৈতিক করিডোর স্থাপন করেছে।
ইতিহাস[সম্পাদনা]
প্রত্নতত্ত্ব[সম্পাদনা]
পূর্ব উপমহাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে লুম্বিনী, গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান; নালন্দা, বিক্রমশিলা, সোমপুর, ওদন্তপুরী, ময়নামতী ইত্যাদি মঠ ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; পাটলিপুত্র, বৈশালী, রাজগির, শিশুপালগড়, কলিঙ্গ ইত্যাদি মৌর্য আমলের অঞ্চল ও বসতিতে অশোক স্তম্ভ; এবং চন্দ্রকেতুগড়, ওয়ারি-বটেশ্বর ও ভিটাগড় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। এই অঞ্চলে এক গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ পর্যটন বর্তনী রয়েছে।[৪] এছাড়াও দক্ষিণ এশিয়ায় অনেক মধ্যযুগীয় মসজিদ রয়েছে, যেমন আদিনা মসজিদ (উপমহাদেশের বৃহত্তম মধ্যযুগীয় মসজিদ), ষাট গম্বুজ মসজিদ, কাটরা মসজিদ ইত্যাদি।
প্রাচীন রাজ্যসমূহ[সম্পাদনা]
পূর্ব দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশীয় সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসাবে পরিচিত। এই অঞ্চলে মহাভারতের মতো প্রাচীন মহাকাব্যে উল্লেখিত বঙ্গ ও পুণ্ড্র; গ্রিক ও রোমান নথিতে উল্লেখিত গঙ্গাঋদ্ধি;[৫] এবং বিভিন্ন প্রধান হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজ্য রয়েছে, যেমন মগধ, অঙ্গ, কলিঙ্গ, বিদেহ, সমতট, নন্দ, মৌর্য, কামরূপ, কাণ্বকুব্জ, গুপ্ত, গৌড়, পাল, সেন, ত্রিপুরা ও কোচবিহার। এই অঞ্চলের অন্যতম ইসলামি সাম্রাজ্য ও রাজ্যের মধ্যে বাংলা সালতানাত, সুরী সাম্রাজ্য, মুঘল সাম্রাজ্য ও সুবে বাংলা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে বারো ভূঁইয়া নামক এক হিন্দু-মুসলিম জমিদার গোষ্ঠী সক্রিয় ছিল।
বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি[সম্পাদনা]
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি স্থাপন করেছিল, যার সদর দপ্তর ফোর্ট উইলিয়াম, কলকাতা। ব্রিটিশরা বাংলাকে তাদের ভারতীয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এবং তখন বাংলা বলতে ভারতকে বোঝাতে লাগল।[৬]
ভূগোল[সম্পাদনা]
উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারত[সম্পাদনা]
স্থলবেষ্টিত উত্তর-পূর্ব ভারত অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয় ও সিকিম রাজ্য নিয়ে গঠিত। পূর্ব হিমালয়, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও বরাক উপত্যকা এই অঞ্চলের অন্তর্গত। ব্রহ্মপুত্র, বরাক ও ইম্ফল উপত্যকা এবং ত্রিপুরা ও মেঘালয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী সমভূমি ছাড়া এই অঞ্চলের বাকি দুই-তৃতীয়াংশ পাহাড়ি এলাকা। উত্তর-পূর্ব ভারতের উচ্চতা প্রায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠের সাপেক্ষে ৭,০০০ মিটার (২৩,০০০ ফুট) পর্যন্ত হত পারে। এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত অনেক বেশি, যার গড় মান ১০,০০০ মিলিমিটার (৩৯০ ইঞ্চি) বা তার বেশি হতে পারে, যার ফলে বাস্তুতন্ত্র, ভূমিকম্প ও বন্যার সমস্যা দেখা দেয়।
পূর্ব ভারতের এক বড় অংশ সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির অন্তর্গত এবং বঙ্গোপসাগর বরাবর এর উপকূলরেখা রয়েছে। সাধারণত ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার রাজ্য এই অঞ্চলের অন্তর্গত। সংকীর্ণ শিলিগুড়ি করিডোর পূর্ব ভারতকে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাথে সংযুক্ত রাখে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবধি বিস্তৃত।
নেপাল[সম্পাদনা]

নেপালের ভূ-প্রকৃতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ নেপালের আকৃতি অনেকটা চতুর্ভুজের মত, প্রায় ৮৮০ কিমি (৫৪৭মাইল) দৈর্ঘ্য এবং ২০০ কিমি (১২৫ মাইল) প্রস্থ। নেপালের মোট আয়তন প্রায় ১৪৭,১৮১ বর্গকিমি (৫৬,৮২৭ বর্গমাইল)। ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্য অনুসারে নেপাল তিন ভাগে বিভক্ত- পর্বত, পাহাড়ী উঁচু ভূমি(Hill and Siwalik region) এবং নিচু সমতল ভূমি অর্থাৎ তরাই।
প্রধান ভৌগোলিক ক্ষেত্র-
দক্ষিণে ভারতের সীমান্তঘেঁষা তরাই নিম্নভূমি নারায়ণী ও কর্ণালী নদীবিধৌত।বাংলাদেশ[সম্পাদনা]

দক্ষিণ এশিয়ার দীর্ঘতম দুটি নদী - গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র যেখানে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে সেখানেই কালের পরিক্রমায় গড়ে ওঠা বঙ্গীয় ব-দ্বীপ। এই গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র মোহনা অঞ্চলে প্রায় ৩০০০ বছর বা তারও পূর্ব থেকে যে জনগোষ্ঠীর বসবাস, তা-ই ইতিহাসের নানান চড়াই উতরাই পেরিয়ে এসে দাড়িয়েছে বর্তমানের স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ রূপে। ভৌগোলিক বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায়, ভারত ও মিয়ানমারের মাঝখানে। এর ভূখণ্ড ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার (বিবিএস ২০২০ অনুসারে)[৭] অথবা ১,৪৮,৪৬০ বর্গকিলোমিটার (সিআইএ ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুক ২০২১ অনুসারে)[৮] এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। বাংলাদেশের পশ্চিম, উত্তর, আর পূর্ব জুড়ে রয়েছে ভারত। পশ্চিমে রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় রাজ্য। পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম। তবে পূর্বে ভারত ছাড়াও মিয়ানমারের (বার্মা) সাথে সীমান্ত রয়েছে। দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের স্থল সীমান্তরেখার দৈর্ঘ্য ৪,২৪৬ কিলোমিটার যার ৯৪ শতাংশ (৯৪%) ভারতের সাথে এবং বাকী ৬ শতাংশ মিয়ানমারের সাথে। বাংলাদেশের তটরেখার দৈর্ঘ্য' ৫৮০ কিলোমিটার। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশের কক্সবাজার পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতগুলোর অন্যতম।
বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩°৫`) অতিক্রম করেছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা সমুদ্র সমতল হতে মাত্র ১০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। সমুদ্র সমতল মাত্র ১ মিটার বৃদ্ধি পেলেই এদেশের ১০% এলাকা নিমজ্জিত হবে বলে ধারণা করা হয়। [৯] বাংলাদেশের উচ্চতম স্থান দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এর মোডকমুয়াল পর্বত, যার উচ্চতা ১,০৫২ মিটার (৩,৪৫১ ফুট)।[১০] বঙ্গোপসাগর উপকূলে অনেকটা অংশ জুড়ে সুন্দরবন অবস্থিত, যা বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। এখানে রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিন সহ নানা ধরনের প্রাণীর বাস। ১৯৯৭ সালে এই এলাকাকে বিলুপ্তির সম্মুখীন বলে ঘোষণা দেয়া হয়। [১১]
বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে ৬টি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে-গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। বছরে বৃষ্টিপাতের মাত্রা ১৫০০-২৫০০মি.মি./৬০-১০০ইঞ্চি; পূর্ব সীমান্তে এই মাত্রা ৩৭৫০ মি.মি./১৫০ইঞ্চির বেশি। বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা ২৫o সেলসিয়াস। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে কর্কটক্রান্তি অতিক্রম করেছে। এখানকার আবহাওয়াতে নিরক্ষিয় প্রভাব দেখা যায়। নভেম্বর হতে মার্চ পর্যন্ত হালকা শীত অনুভূত হয়। মার্চ হতে জুন মাস পর্যন্ত গ্রীষ্ম কাল চলে। জুন হতে অক্টোবর পর্যন্ত চলে বর্ষা মৌসুম। এসময় মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, ও জলোচ্ছাস প্রায় প্রতিবছরই বাংলাদেশে আঘাত হানে।ভুটান[সম্পাদনা]
ভুটানের আয়তন ৪৬,৫০০ বর্গকিলোমিটার। থিম্পু এর রাজধানী শহর এবং এটি দেশের মধ্য-পশ্চিম অংশে অবস্থিত। অন্যান্য শহরের মধ্যে পারো, ফুন্টসলিং, পুনাখা ও বুমথং উল্লেখযোগ্য। ভুটানের ভূপ্রকৃতি পর্বতময়। উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় পর্বতমালা, মধ্য ও দক্ষিণভাগে নিচু পাহাড় ও মালভূমি এবং দক্ষিণ প্রান্তসীমায় সামান্য কিছু সাভানা তৃণভূমি ও সমভূমি আছে। মধ্যভাগের মালভূমির মধ্যকার উপত্যকাগুলিতেই বেশির ভাগ লোকের বাস। ভুটানের জলবায়ু উত্তরে আল্পীয়, মধ্যে নাতিশীতোষ্ণ এবং দক্ষিণে উপক্রান্তীয়; জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়। স্থলবেষ্টিত দেশ ভুটানের আকার, আকৃতি ও পার্বত্য ভূ-প্রকৃতি সুইজারল্যান্ডের সদৃশ বলে দেশটিকে অনেক সময় এশিয়ার সুইজারল্যান্ড ডাকা হয়।
বহির্বিশ্ব থেকে বহুদিন বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে ভুটান প্রাণী ও উদ্ভিদের এক অভয়ারণ্য। এখানে বহু হাজার দুর্লভ প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়। ভুটানের প্রায় ৭০% এলাকা অরণ্যাবৃত। এই অরণ্যই ভুটানের জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে চলেছে যুগ যুগ ধরে।জনপরিসংখ্যান[সম্পাদনা]
| ক্রম | পূর্ব দক্ষিণ এশিয়া | জনসংখ্যা | ক্রম | পূর্ব দক্ষিণ এশিয়া | জনসংখ্যা | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ঢাকা  কলকাতা |
১ | ঢাকা | বাংলাদেশ | ২,২৪,৭৮,১১৬ | ১১ | গুয়াহাটি | ভারত | ১১,৫৫,০০০ |  চট্টগ্রাম  পাটনা |
| ২ | কলকাতা | ভারত | ১,৫১,৩৩,৮৮৮ | ১২ | শিলিগুড়ি | ভারত | ১০,৯২,০০০ | ||
| ৩ | চট্টগ্রাম | বাংলাদেশ | ৫২,৫২,৮৪২ | ১৩ | খুলনা | বাংলাদেশ | ৯,৫০,০০০ | ||
| ৪ | পাটনা | ভারত | ২৫,২৯,২১০ | ১৪ | রাজশাহী | বাংলাদেশ | ৯,৪২,০০০ | ||
| ৫ | জমশেদপুর | ভারত | ১৬,৬১,০০০ | ১৫ | সিলেট | বাংলাদেশ | ৯,২৮,০০০ | ||
| ৬ | কাঠমান্ডু | নেপাল | ১৫,২১,০০০ | ||||||
| ৭ | রাঁচি | ভারত | ১৫,১১,০০০ | ||||||
| ৮ | আসানসোল | ভারত | ১৪,৭৮,২৬৬ | ||||||
| ৯ | ধানবাদ | ভারত | ১৩,৬৮,০০০ | ||||||
| ১০ | ভুবনেশ্বর | ভারত | ১২,২৬,০০০ | ||||||
নেপাল[সম্পাদনা]
নেপালের জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ এবং এটি ৪১শ (একচত্বারিংশ) সবচেয়ে জনবহুল দেশ। নেপাল এক বহুজাতিক হিমালয় রাষ্ট্র, যার সরকারি ভাষা নেপালি।
বাংলাদেশ[সম্পাদনা]
বাংলাদেশের জনসংখ্যা ২০২২ জনশুমারি অনুযায়ী জুন, ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬,৫১,৫৮,৬১৬ ( ১৬ কোটি ৫১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬১৬ জন)।[১২]এটি বিশ্বের ৮ম বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ। এখানে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ১,১১৯ জন, যা সারা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ (কিছু দ্বীপ ও নগর রাষ্ট্র বাদে)। এখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%[১৩] । বাংলাদেশে পুরুষ ও নারীর অনুপাত ১০০.৩:১০০[১৩]। দেশের অধিকাংশ মানুষ শিশু ও তরুণ বয়সী (০–২৫ বছর বয়সীরা মোট জনসংখ্যার ৬০%, ৬৫ বছরের বেশি বয়সীরা মাত্র ৬%)। এখানকার পুরুষ ও মহিলাদের গড় আয়ু ৭২.৩ বছর।[১৪] জাতিগতভাবে বাংলাদেশের ৯৮% মানুষ বাঙালি। বাকি ২% মানুষ বিহারী বংশদ্ভুত, অথবা বিভিন্ন উপজাতির সদস্য। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ১৩টি উপজাতি রয়েছে। এদের মধ্যে চাকমা উপজাতি প্রধান। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের উপজাতি গুলোর মধ্যে গারো ও সাঁওতাল উল্লেখযোগ্য। দেশের ৯৮% মানুষের মাতৃভাষা বাংলা, যা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। সরকারি কাজ কর্মে ইংরেজিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে ১৯৮৭ সাল হতে কেবল বৈদেশিক যোগাযোগ ছাড়া অন্যান্য সরকারি কর্মকান্ডে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর প্রধান ধর্মবিশ্বাস ইসলাম (৯০.৪%)।[১৫] এরপরেই রয়েছে হিন্দু ধর্ম(৮.৫%), বৌদ্ধ (০.৬%), খ্রীস্টান (০.৩%) এবং অন্যান্য (০.১%)।[১৬]মোট জনগোষ্ঠীর ২১.৪% শহরে বাস করে, বাকি ৭৮.৬% গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী। সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন কর্মকান্ডের ফলে দারিদ্র বিমোচন ও জনসাস্থ্যে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক দৈনিক মাত্র ১ মার্কিন ডলার আয় করে (২০০৫)।[১৭] আর্সেনিক জনিত বিষক্রিয়া বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সমস্যা।[১৮] এছাড়া বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে। ২০১৭ এর পরে এরোগ আর দেখা য়ায় না বলেই চলে। ২০০৫ সালের হিসাবে বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার প্রায় ৪১%।[১৯] ইউনিসেফের ২০০৪ সালের হিসাবে পুরুষদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার ৫০% এবং নারীদের মধ্যে ৩১%।[২০]
তবে সরকারের নেয়া নানা কর্মসূচীর ফলে দেশে শিক্ষার হার বাড়ছে। এর মধ্যে ১৯৯৩ সালে শুরু হওয়া শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করেছে।[২১] এছাড়া মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে বৃত্তি প্রদান কর্মসূচী নারীশিক্ষাকে এগিয়ে নিচ্ছে।[২২]ভারত[সম্পাদনা]
উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতের মোট জনসংখ্যা প্রায় ২৭ কোটি এবং সেখানে বহুজাতিক ও বহুভাষিক ইন্দো-আর্য ও তিব্বতি-বর্মীয় জনগোষ্ঠী রয়েছে। কলকাতা, পাটনা, জমশেদপুর, রাঁচি, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি, শিলিগুড়ি, শিলং, আগরতলা ইত্যাদি এখানকার বৃহত্তম শহর। কেন্দ্রীয় স্তরে হিন্দি ও ইংরেজি ভাষা সরকারি হলেও বেশিরভাগ রাজ্যের নিজস্ব সরকারি ভাষা রয়েছে।
ভুটান[সম্পাদনা]
জনসংখ্যা অনুযায়ী মালদ্বীপের পর ভুটান দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম দেশ। বহুজাতিক ভুটানের রাষ্ট্রধর্ম বৌদ্ধধর্ম ও সরকারি ভাষা জংখা। এছাড়া ভুটানে নেপালিভাষী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে। থিম্ফু ও ফুন্টসলিং এই দেশের বৃহত্তম শহর।
আরও দেখুন[সম্পাদনা]
তথ্যসূত্র[সম্পাদনা]
- ↑ "Sub-Regional Relations in the Eastern South Asia: With Special Focus on India's North Eastern Region - Joint Research Program Series No.133 - Institute of Developing Economies"। Ide.go.jp। ২০১৭-০৮-১৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১৭-০৭-১৮।
- ↑ Ambassador Rajiv Bhatia; Mr Swaran Singh; Ms Reena Marwah (১৫ নভেম্বর ২০১৩)। Transforming South Asia: Imperatives for Action: Imperatives for Action। KW Publishers Pvt Ltd। পৃষ্ঠা 61–। আইএসবিএন 978-93-85714-61-0।
- ↑ Sadiq Ahmed; Saman Kelegama; Ejaz Ghani (২ ফেব্রুয়ারি ২০১০)। Promoting Economic Cooperation in South Asia: Beyond SAFTA। SAGE Publications। পৃষ্ঠা 140। আইএসবিএন 978-81-321-0497-1।
- ↑ "International conference on Developing Sustainable and Inclusive Buddhist Heritage and Pilgrimage Circuits in South Asia's Buddhist Heartland in collaboration with UNWTO | Regional Programme for Asia & the Pacific"। Asiapacific.unwto.org। ২০১৭-০৭-২৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১৭-০৭-১৮।
- ↑ Tim Steel (২০১৬-১২-১০)। "The Greeks wrote about these lands"। Dhaka Tribune (Opinion)। ২০১৭-০৬-২৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১৭-০৭-১৮।
- ↑ "India, your name could be Bangladesh"। Dhaka Tribune। ২০১৭-০৭-২৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১৭-০৭-১৮।
- ↑ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০২০ (পিডিএফ)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। পৃষ্ঠা ২১। আইএসবিএন ৯৭৮-৯৮৪-৪৭৫-০৪৭-০।
- ↑ "South Asia :: Bangladesh — The World Factbook – Central Intelligence Agency"। www.cia.gov। ২০২১-১১-১৩ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-১১-১৩।
- ↑ Ali, A (১৯৯৬)। "Vulnerability of Bangladesh to climate change and sea level rise through tropical cyclones and storm surges"। Water, Air, & Soil Pollution। 92 (1-2): 171–179।
- ↑ Summit Elevations: Frequent Internet Errors. ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ২৫ জুলাই ২০১৩ তারিখে Retrieved 2006-04-13.
- ↑ IUCN (১৯৯৭)। "Sundarban wildlife sanctuaries Bangladesh"। World Heritage Nomination-IUCN Technical Evaluation।
- ↑ "জনসংখ্যা সাড়ে ১৬ কোটি, নারীর সংখ্যা বেশি, কমেছে হিন্দু জনগোষ্ঠী"। বিবিসি বাংলা। সংগ্রহের তারিখ ২০২২-০৭-২৭।
- ↑ ক খ Bangladesh Sample Vital Statistics 2018 (পিডিএফ)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ২০১৯। পৃষ্ঠা ৩১। আইএসবিএন 978-984-34-6845-1।
- ↑ "ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুক"। The World Factbook। ১৩ জানুয়ারি ২০২০। ২৫ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৩ জানুয়ারি ২০২০।
- ↑ Center, Pew Research (27 জানু, 2011)। "Table: Muslim Population by Country"। এখানে তারিখের মান পরীক্ষা করুন:
|তারিখ=(সাহায্য) - ↑ "সংরক্ষণাগারভুক্ত অনুলিপি"। ২০১৪-১২-২৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০১৫-০৮-২৪।
- ↑ "Congressional Budget Justification – FY 2005"। USAID। ২৮ জুলাই ২০০৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৬।
- ↑ Nickson, R (১৯৯৮)। "Arsenic poisoning of Bangladesh groundwater"। Nature (6700): 338। অজানা প্যারামিটার
|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - ↑ "2005 Human Development Report"। UNDP। ৩১ অক্টোবর ২০০৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৬।
- ↑ "UNICEF: Bangladesh Statistics"। ১৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৬।
- ↑ Ahmed, A (২০০২)। The food for education program in Bangladesh: An evaluation of its impact on educational attainment and food security, FCND DP No. 138। International Food Policy Research Institute। অজানা প্যারামিটার
|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য) - ↑ Khandker, S (২০০৩)। Subsidy to Promote Girls’ Secondary Education: the Female Stipend Program in Bangladesh। World Bank, Washington, DC। অজানা প্যারামিটার
|coauthors=উপেক্ষা করা হয়েছে (|author=ব্যবহারের পরামর্শ দেয়া হচ্ছে) (সাহায্য)